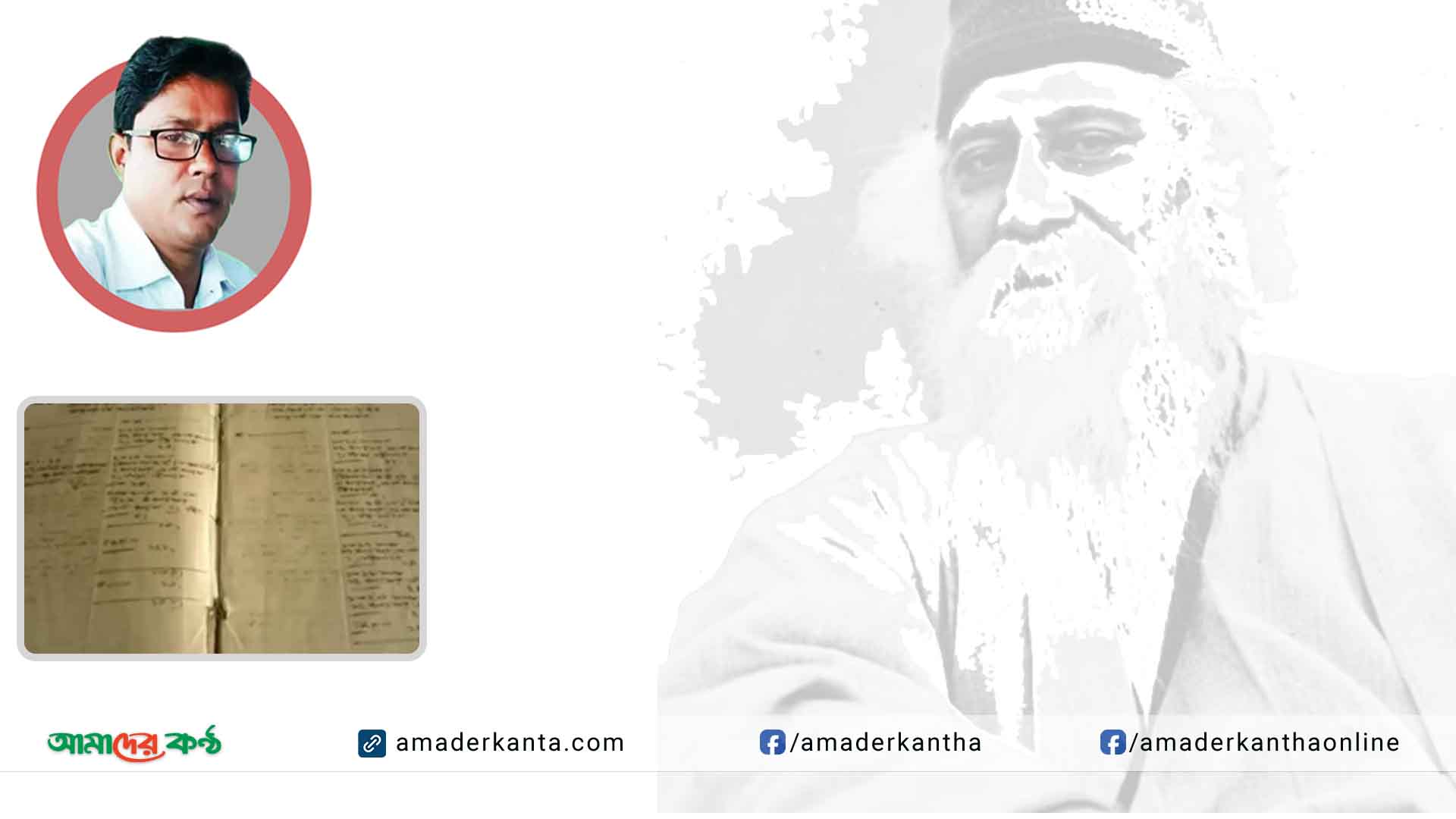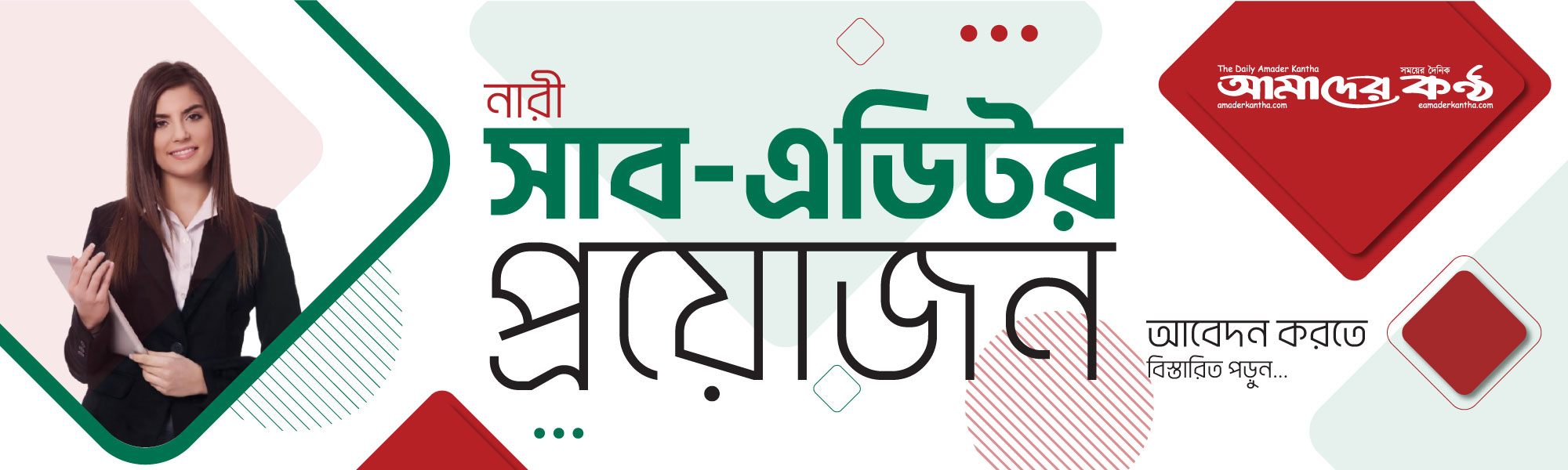এম মতিউর রহমান মামুনঃ
পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি সমবায় ব্যাংক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুদখোর মহাজনের হাত থেকে গরীব অসহায় হতদরিদ্র প্রজাদের মুক্ত করা এবং তাই হয়েছিল। ১৯০৫ সালে ধারদেনা করে প্রথম ব্যাংক খুলেছিলেন পরে নবেল প্রাপ্তির পর সব টকা গরীবপ্রজাদের মাঝে স্বল্পসুদে ঋণ দিলেন আর মহাজন’রা এলাকা ছাড়লো। দাসস্তগোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত হল কালীগ্রাম পরগণাবাসী। অন্যদিকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা সম্ভব হয়েছিল । অথ্যাৎ অর্থ বৃত্তের সঙ্গে শিক্ষার যোগসুত্র বোধ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসরে কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন।
পতিসরে এসে দারিদ্রপীড়িত গ্রামবাসীকে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক- একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়ে আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যাবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যাবহার-সামগ্রী সন্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত করো’।( রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খন্ড )। কালীগ্রাম পরগনার পল্লীগঠণের কাজে হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। শোষিত বঞ্চিত কৃষকদের বাস্তব অবস্থা অবলোকন করে এক চিঠিতে লিখলেন ‘কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখ দৈন্য-নিবেদন! এদের অকৃতিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জ্বল আসে।… বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক” (ছিন্নপত্র ১১১)। পতিসর থেকে অপর এক চিঠিতে লিখেছেন ‘অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকান্না -ওয়ালা সরল হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানেনা। আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত’।(ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ১৩৯৯ পৃষ্টা ৩৭) রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কৃষক সমাজ মহাজনদের কাছে তাঁরা ঋণী, এখান থেকে মুক্ত করতে না পারলে তাঁদের পক্ষে কোন কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। সেই লক্ষে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজনের কাছে ধার দেনা করে (১৯০৫) পতিসর ব্যাংক খুললেন নাম ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক’ উদ্দেশ্য স্বল্প সুদে প্রজাদের টাকা ধার দিয়ে মহাজনের গ্রাস থেকে তাঁদের মুক্ত করে অর্থবৃত্তে স্বাবলম্বী করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া দারিদ্র, অস্বাস্থ ও অজ্ঞতা দূর করিতে পারে—প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি…..আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায়..এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যায় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে’ (পল্লীপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ২৬১)
তাই গবেষকরা মনে করেন, ‘রবীন্দ্রনাথের পল্লীসমাজ পরিকল্পনার সর্বত্তোম প্রকাশ যদি গণতান্ত্রিক গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যাবস্থায় এবং এর অর্থনৈতিক ভিত্তি সর্বজনীন সমবায় ব্যাবস্থায় ঘটে থাকে, তাহলে সে সমবায় চিন্তার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক স্থাপনে। আমাদের ভেবে দেখা দরকার রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ছিল এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম সোপান, তার প্রকাশ পতিসরের কৃষি সমবায় ব্যাংক। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামের শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা ভয়াবহ মহাজনী ঋণের কবল থেকে মুক্তি পেল, কৃষক -কৃষির উন্নতি হলো, গ্রামের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেল স্বাস্থ সেবার উন্নয়ন হলো । রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠি ছিল একটি অসাধারণ মাইলফলক’ (রবীন্দ্র ভূবনে পতিসর আহমদ রফিক)। রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শত বছর পরে আমাদের দেশে গ্রামীণ মানুষের উন্নতির জন্য বে-সরকারী কিছু সংস্থা (এন,জি, ও) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচী দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, শত বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন ও পল্লীগঠণের কাজে কি গভীর অন্তদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন পতিসরে। বৃটিশ ভারতে যখন সমবায় কার্যক্রম শুরু হয়নি ব্যাংক ব্যাবস্থা নেই বললে চলে, কোঅপারেটিভ ব্যাংক, লোন কম্পানি যখন ছিলোনা তখন পতিসরের মতো অখ্যাত পল্লীগ্রামে কৃষি ব্যাংক খুলে কৃষকদের ঋণমুক্ত হতে সহযোগিতা করা শুধু অসান্য কর্মদক্ষতাই নয় বরং ক্ষুদ্র ঋণের গোড়াপত্তন করে অসান্য অবদান রেখে গেছেন।
ব্যাংক চলেছিলো পঁচিশ বছর বাংলা১৩২০ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত ( সম্প্রতি আমার উদ্ধার কৃত বরীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকের লেজারের হিসাব অনুযায়ী) আর অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, “ব্যাংক চলেছে কুড়ি বছর। ” প্রথমে ধারদেনা করে ১৯০৫ সালে পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করার পর কৃষকদের মধ্যে ব্যাংক এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, তাঁদের ঋণের চাহিদা মিটানো স্বল্প শক্তির এ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। অবশ্য সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় নোবেল পুরস্কারের টাকা ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে কৃষি ব্যাংকে জমা হওয়ার পর। কত টকা ব্যাংকে মূলধোন ছিল তা নিয়েও মতোভেদ আছে কেউ বলছেন এক লক্ষ আট হাজার আবার অনেকে লিখেছেন এক লক্ষ আটাত্তোর হাজার টাকা’। (রবীন্দ্র জীবনী প্রশান্ত কুমার পাল ২য় পৃ. ৪৬২)। শুধু নবেল আর ধারদেনার টাকাই নয়, ব্যাংকের অবস্থা অস্থিতিশীল দেখে ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের রিয়্যালটি এবং আমেরিকায় বক্তৃতা বাবদ প্রাপ্ত টাকা থেকে ন’হাজার টাকা জমা দেন। তবুও শেষ পর্যন্তু ব্যাংক আর টিকলোনা। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পিতৃস্মৃিতি’তে লিখেছেন ‘ ব্যাংক খোলার পর বহু গরীর প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হওয়ার। কৃষি ব্যাংকের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural indebtedness – (গ্রামীণ ঋণ) এর আইন প্রবর্তন হলো। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায়ের উপায় রইল না’। ব্যাংকের শেষ অবস্থা নিরীক্ষণ করে ১৯১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে কবিগুরু প্রমথ চৌধুরীকে বার বার অনুরোধ করে লিখেছেন “দোহায় তোমার যত শ্রীঘ্র পার ব্যাংটাকে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিতে পরিণত করে নাও” ( রবীন্দ্র জীবনী প্রশান্ত কুমার পাল খন্ড ৭ পৃষ্টা ২৯৭) কিন্তু কবির সে অনুরোধ শতর্কবাণী রাখা হয়নি, ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সকল স্বপ্ন শেষ করে দিয়ে।
কালীগ্রামের এসব কর্মযজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ সফল হয়েছিলেন তা কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় “সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রাম বাসীদের অবস্থার অন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠলো। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছেনা। দেখলুম-নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল স্কুলের ঘাটে। এমনকি, আট দশ মাইল দুরের গ্রাম খেকে ও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেনীর কোন ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। হাসপাতাল ও ডিসস্প্রেনছাড়ির কাজ ভালো চলছে। যেসব জোলা আগে এক সময গামছা বুনত তাঁরা এখন ধুতি, শাড়ী, বিছানার চাদর বুনতে পারছে। কুমোড়দের ও কাজের উন্নতি হয়েছে গ্রাম বাসির আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। শুধু চাষীরা অণুযোগ জানালো তাদেরকে চাষের জন্য আরও ট্রাক্টর এনে দেওয়ার জন্য” (পিতৃস্মৃতি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
রবীন্দ্র পরবর্তী পতিসর কাচারী বাড়ি থেকে ব্যাংকের মূল্যবান নথিপত্র সহ সমস্ত রবীন্দ্রস্মৃতি চিহ্ন হারিয়ে যায়। সেই সমস্ত মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন পূনরায় উদ্ধার করে পতিসরে পূর্ণঙ্গ রবীন্দ্র মিউজিয়াম করার চেষ্টা করেছি। অনেক গুরুত্বপূর্ন রবীন্দ্রস্মৃতি উদ্ধার করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করেছি। কবির লেখা ছয় পৃষ্ঠার চিঠি, কবি প্রতিষ্ঠত ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংকের হিসাবের খাতা, কালীগ্রামের শেষ জমিদার কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও পুত্র বধু প্রতিমা দেবী’র মূল্যবান বেশ কিছু চিঠি, কবির ব্যাবহৃত খাট, টি পট, আলমারী, ওয়্যারড্রব, নাগোর বোটের দরজা-জানালা সহ সমমানের আরও নির্দশন । লেজার টি উদ্ধার করেছিলাম রাণীনগরে বিলকৃষ্ণপুর নিবাস মোহাম্মদ আহম্মদ আলী শাহ্ নাত জামাই কলেজ শিক্ষক আব্দুল হামিদের বাসা থেকে, বলে রাখা দরকার তিনি রবীন্দ্রনাথের কৃষি ব্যাংকই কর্মরত ছিলেন। মূল্যবান খাতা হাতে আসার পর জানতে পারলাম এমন লেজার দুই রাংলার কোথায় নেই। পতিসর কৃষিব্যাংকের তথ্যাদি শুধু গবেষকদের কলমেই ছিল, বাস্তব এ ধরণের দালিলিক প্রামান ছিলনা। পরিতাপের বিষয রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাংকের এই দুর্লভ খাতাটি কেনার জন্য সভ্যসংস্কৃতির দেশের মানুষ মরিয়া হয়েছিল কিন্তু আমার নীতিতে আমি অটল ছিলাম। যাহোক লেজারটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০৯ সালের ৮ মে ২৫ বৈশাখ তৎকালীন নওগাঁর জেলাপ্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করেছিলাম পরে মূল্যবান লেজার জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। আজ দেশ ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ লেজারটি গবেষণায় নেওয়ার জন্য বাব বার পতিসরে ছুটে এসে না দেখার যন্ত্রনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।
মহামূল্যবান এই লেজারটি পতিসর মিউজিয়ামে সংরক্ষণ অতি জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।
লেখক: রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রাহক ও গবেষক
প্রতিষ্ঠাতা, রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রহশালা।